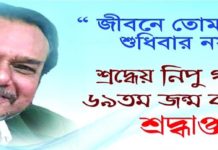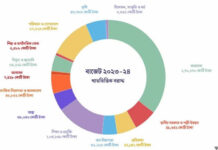শিরোনাম :
পার্বত্য বান্দরবান: সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি
নয়ন যোসেফ গমেজ, সিএসসি:
নয়নলোভন ষড়ঋতুর অপূর্ব লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এখানে একেক ঋতুতে প্রকৃতি একেক রূপ ধারণ করে। এভাবে পুরো বছর জুড়েই আমাদের দেশে বিরাজ করে প্রকৃতির রকমারি রূপ-লাবণ্য। এরই মাঝে এই বছরের শুরুতে অর্থাৎ মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাক্কালে রাজধানী ঢাকার রামপুরার বনশ্রীতে অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহ থেকে আমরা চব্বিশ জনের একটি দল সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি বান্দরবান ভ্রমণ করে এলাম। তখনও বহুরূপী মহারানী করোনা আমাদের দেশে তার এমন বিধ্বংসী প্রভাব বিস্তার করেনি। আমরা তখনও আমাদের মতই ছিলাম। আর তাই আমাদের সবকিছুই চলছিল আমাদের মত করেই। আমাদের ভ্রমণটাও ছিল স্বাভাবিক। সেদিন আমাদের বাসযাত্রা আরম্ভ হয়েছিল মতিঝিলের নটর ডেম কলেজের সামনে থেকে। রাত এগারোটা নাগাদ আমাদের বহণকারী বাসটি ছেড়ে যায়। ভোর ছয়টা নাগাদ আমরা বান্দরবান সদরে অবতরণ করি। আমাদের জন্য বান্দরবান সদরের বাসস্ট্যান্ডে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। স্থানীয় ভাষায় ঐ গাড়িগুলোকে বলা হয় চান্দের গাড়ি। তো সেই চান্দের গাড়িতে করেই আমরা বান্দরবান ক্যাথলিক গির্জায় পৌঁছাই। গির্জা ক্যাম্পাসে আমাদের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুণছিলেন গির্জার পাল-পুরোহিত ফাদার বিনয় গমেজ, সিএসসি। সেখানে আমাদের জন্য সকালের নাস্তা প্রস্তুত ছিল। আমরা সারা রাত্রির ক্লান্তি কাটিয়ে সবাই একটু ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করি। নাস্তার পরপরই আমাদের যাত্রা শুরু হয় থানচির উদ্দেশ্যে। রাতে বাসের ভেতর থাকার দরুণ বান্দরবানের কিছুই দেখিনি। কিন্তু এবার আর যায় কোথায়! বান্দরবান মিশন ক্যাম্পাস হতে থানচি। পুরো চার ঘন্টার পাহাড়ি রাস্তা। পাহাড়ি রাস্তা হলে কি হবে সম্পূর্ণই পীচঢালা কলো রাস্তা।
আমরা সকলে চান্দের গাড়িতে রওনা হয়েছি।
চান্দের গাড়ির বিশেষত্ব হল এই গাড়িগুলো সবদিকে খোলা। ভেতরে বসলে পুরো চারপাশ অবলীলায় অবলোকন করা যায়। থানচি যেতে যেতে বান্দরবানের সৌন্দর্য দু’চোখ ভরে দেখছিলাম। যেন আস্বাদন করছিলাম! মাঝে মাঝে নিজের চোখকেই যেন বিশ^াস করতে পারছিলাম না! বারংবার মনে হচ্ছিল এ আমাদের বাংলাদেশ নয়। এ অন্য কোন দেশ! অন্য কোন রাজ্য! যেন স্বপ্নের কোন সাম্রাজ্য। থানচি যেতে যেতে আমার বারবার মনে পড়ছিল আমাদের গ্রামের চিকনাই নদীটির দু’পাড়ের কথা। আমি সমতল এলাকার সন্তান। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বরেন্দ্রভূমি রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার চাটমোহরের কদমতলী গ্রামে আমার জন্মভিটা ও বাড়ি। চাটমোহর স্বভাবতই সমতল ও বিল-প্রধান। এখানকার চলনবিল বিশ^-খ্যাত। আমাদের গ্রামটিও সমতল এবং বিল-প্রধান। বিলের মাঝে মাঝে আমাদের গ্রামগুলো। আমাদের গ্রামের মূল নদীটি গ্রামের মানচিত্রে চিকনাই নদী নামে খ্যাত। অথচ আমরা সেই নদীকে যুগ যুগ ধরে গাঙ বলেই জানি। গাঙের শাখানদী বয়ে গেছে আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে। আমরা ঐ শাখা -নদীকে জোলা নামে চিনি। জোলার পাড়টাও বেশ উঁচু। শৈশবে জানতাম গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা আমাদের নদীর পাড়। ওহ্! আসল কথায় আসা যাক! বান্দরবানের পাহাড়ি রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে পাহাড়ের মধ্য দিয়েই। আমাদের চান্দের গাড়ি রকেটের মত ছুটে চলছিল।
-নদীকে জোলা নামে চিনি। জোলার পাড়টাও বেশ উঁচু। শৈশবে জানতাম গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জায়গা আমাদের নদীর পাড়। ওহ্! আসল কথায় আসা যাক! বান্দরবানের পাহাড়ি রাস্তাগুলো এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে পাহাড়ের মধ্য দিয়েই। আমাদের চান্দের গাড়ি রকেটের মত ছুটে চলছিল।
পাহাড়ি রাস্তা! তাতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সহজে ব্যক্ত দুষ্কর! আসলে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা কখনোই বলে-কয়ে বুঝানো যায় না ! নিজে অভিজ্ঞতা করে তবে বুঝে নিতে হয়। পাহাড়ি পথে চলতে চলতে আমাদের গাড়ি কখনো শোঁ-শোঁ করে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছিল। আবার হঠাৎ সাঁই-সাঁই করে একবারে নিচে নেমে আসছিল। যখন গাড়িটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তখন সমস্ত এলাকা নিচে দেখা যায়। তবে আমি অবাক হলাম প্রায় প্রতিটি পাহাড়ের ঢালুতেই মানুষের বসতি। কোথাও ত্রিপুরাপাড়া আবার কোথাও ক্ষুমি, বম বা মারমাপাড়া। পাহাড়ের সাথে সংগ্রাম করেই অতিবাহিত হয় তাদের দৈনন্দিন জীবন। রাস্তায় যাদের দেখলাম তাদের সবার হাতেই বিশেষ ধরণের দা আর পিঠে ঝুড়ি; যা কিনা মাথায় ঝুলানো। পাহাড়ে গ্রামগুলোকে বলা হয় পাড়া। আর পাড়া মানেই একসাথে কয়েকটি পরিবারের বসবাস। পাহড়ে স্বাদু পানির একমাত্র উৎস ঝিড়ি। ঝিড়ি হল পাহাড়ের পাদদেশে সবচেয়ে নিচু জায়গা, যেখানে পানি জমে থাকে বা কোন নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। সেই ঝিড়ি থেকেই পাড়ার মানুষ দলবেঁধে গিয়ে ব্যবহার্য পানি সংগ্রহ করে আনে। দিনে কয়েকবার চলে এই পানি উত্তোলনের কাজ। কোন বাড়িতেই টিউবওয়েল নেই। তবে কিছু কিছু বাড়িতে দেখলাম পানির সরু পাইপ; যা কিনা ঝিড়ির সাথে সংযুক্ত করা। বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকার বেশির ভাগ পাড়া বা বাড়িই রাস্তার সঙ্গে লাগোয়া। বান্দরবান হতে থানচি যাবার পথে বেশ কিছু খ্রিস্টানপাড়া চোখে পড়ল। দেখে-ই বুঝা যায় খ্রিস্টান পাড়া বা বাড়ি। কেননা ঘরের চালা বা বেড়ায় ক্রুশ চিহ্ন। কোথাও আবার রাস্তার সাথেই সেই পাড়ার গির্জা। প্রতিটি পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে দেখলাম জুমের চাষাবাদ। আমরা যেহেতু সকালে বান্দরবান হতে থানচি যাচ্ছিলাম, সেহেতু সহজেই নজরে এলো জুম চাষে পাহাড়ি মানুষের কর্মব্যস্ততা। খাঁড়া খাঁড়া পাহাড়ের জঙ্গল পরিস্কার করে পাহাড়িরা জুম চাষ করে থাকে। এই জুমের ফসলই তাদের সাড়া বছরের অবলম্বন। তবে বছরে কয়েকবার তারা জুম চাষ করে থাকে। স্পষ্ট মনে আছে, প্রাথমিক স্কুল জীবনে কোনো এক ক্লাশে পড়েছিলাম পাহাড়িদের জুম চাষের কথা। জুম শব্দটির সাথে তখন থেকেই পরিচয়। কোথাও কোথাও দেখলাম জুমের জন্য জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। এজন্য তারা জঙ্গল কেঁটে আগুনে পুড়াচ্ছে। আগুন আর ধোঁয়া অনেক দূর হতেই দেখা যাচ্ছিল। আবার কেউ জুম কেঁটে ঘরে ফিরে আসছিল। আরেকটি বিষয়ে আমি অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, প্রায় প্রতিটি পাড়াতেই ছোট ছোট দোকান আছে। দোকানে হালকা পাতলা কিছু জিনিস পত্র। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এরা দোকানের জিনিসপত্র পায় কোথায়? কোথা থেকেই বা নিয়ে আসে? নাকি নিজেরাই তৈরি করে? পুরো পাহাড়ি রাস্তায় কেবল আমাদের গাড়িই ছুটে চলেছে। অন্য কোন গাড়ি নেই। আর হাজার কান্নাকাটি করলেও এই পথে আর কোন গাড়ি পাওয়া যাবে না। পাহাড়ি পথে চলতে চলতে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল সাধু যোসেফ আর সন্তান-সম্ভবা কুমারী মারীয়ার কথা। পবিত্র বাইবেলে পড়েছি তারা নাম লেখাবার জন্য পাহাড়ি পথেই নাজারেথ থেকে যুদেয়ায় গিয়েছিলেন। আবার শিশু যিশুকে সঙ্গে নিয়ে বেথলেম হতে মিশর দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন এই পাহাড়ি পথেই! মনে পড়ছিল প্রভু যিশু খ্রিষ্টের জীবনের কথা! প্রভু যিশুরও দিব্য রূপান্তর হয়েছিল তাবর পর্বতের চূড়ায়। তিনি দিন-রাত ধ্যান ও প্রার্থনা করেছেন জৈতুন পর্বতে। শেষে তাঁকে ক্রুশেও দেওয়া হয়েছিল কালভেরী পাহাড়ের চূড়ায়। বান্দরবানের পাহাড়-পর্বত দেখে আমার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি সেই তাবর পর্বত! এই বুঝি সেই কালভেরী! আর ঐ বুঝি সেই জৈতুন চূড়া! সেসব ভাবতে ভাবতে অবশেষে আমরা থানচি পৌঁছলাম।
চান্দের গাড়ি হতে অবতরণ করলাম সাঙ্গু নদীর সেতুর উপর। সেতু লাগোয়া ঐতিহ্যবাহী থানচি বাজার। অল্প সময় থানচি বাজারে অতিবাহিত করলাম। আমদের পরবর্তী গন্তব্য বড় পাথর দেখতে যাওয়া। বড় পাথরের আরেক নাম রাজা পাথর। আমরা সাঙ্গু নদী দিয়ে রাজা পাথর দেখতে যাব। কেননা রাজা পাথর একবারে সাঙ্গু নদীর বুকে। সাঙ্গু বান্দরবানের বিখ্যাত নদী। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই উৎপত্তি এবং বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যেই সমাপ্ত যে দুটি নদী বাংলাদেশে রয়েছে তার মধ্যে সাঙ্গু একটি। এসময় নদীটিতে তেমন পানি নেই। নদীতে পানির পরিমান কোমর-সমান। মাঝে মাঝে হয়তো বুক অবধি। তবুও এরই মাঝে নৌকা চলছে। থানচি বাজার হতে ভেতরের পাড়াগুলোতে যেতে হলে এই নদী পথেই যেতে হবে। নদীতে পানি থাকলে কপাল ভাল। না থাকলে নদীর বুক চিরে হেঁটে যেতে হয়। সাঙ্গু নদীতে সাড়ি সাড়ি বেঁধে রাখা নৌকাগুলো আমাদের ডিঙি নৌকার মতই কিন্তু একটু সরু ও বেশ লম্বা। আবার প্রতিটি নৌকায়-ই পেছনে মোটর লাগানো। আমরা পাঁচটি নৌকা নিয়ে ছুটে চললাম রাজা পাথরের দিকে। নদীর বুকে নৌকাগুলোও ছুটছে ঠিক চান্দের গাড়ির মতই। রকেট বেগে! যদিও নদীর মাঝে মাঝে রয়েছে ভয়ংকর বাঁক। আসলে পাহাড়ি এলাকার সবকিছুর গতি বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা হতে যেন একটু বেশি-ই। পুরো নদীতে পাথর আর পাথর।
সাঙ্গু নদী পাথুরে নদী। যেন পাথরের সাম্রাজ্য! কোথাও বড় বড় পাথর খন্ড। এই পাথরের ফাঁক-ফোকর দিয়েই ছুটে চলছে আমাদের নৌকাগুলো। ছোট আর মাঝারি পাথরের ওপর শ্যাওলার আধিপত্য। নদীর পানি আয়নার মত ঝকঝকে-তকতকে পরিষ্কার। আর প্রচুর ঠান্ডা। নদীর দু’পাড়ে সুউচ্চ খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে দিয়েই বয়ে গেছে সাঙ্গু নদী। আর খাড়া খাড়া পাথরের পাহাড়েই চোখে পড়ল বড় বড় পাহাড়ি গাছ। গাছগুলো মাটির সন্ধান পেয়েছে কিনা জানিনা। তবে পাথরকেই আকড়ে ধরে যুগের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় গাছের শিকড়ই পাথর বেয়ে নদীতে এসে থেমে গেছে। হয়তো এই নদীই তাদের প্রাণের অস্তিত্ব দান করছে। নদীর বুকে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল আদিবাসী মানুষের কর্মব্যস্ততা। পুরুষেরা গাছ ও বাঁশ কেঁটে একসাথে বেঁধে ভেলার মত ভাসিয়ে নিয়ে আসছে। সেই ভেলার দৈর্ঘও বেশ লম্বা। আর নারীরা দল বেঁধে নদীতে নানা পদের শামুক ও ঝিনুক কুড়াচ্ছে। এই ঝিনুক ও শামুক তাদের জন্য বেশ মজাদার খাবার। সাঙ্গু নদীর যে বিষয়টি আমাকে চরম ভাবে বিষ্মিত করল তা হল যে, সম্পূর্ণ সাঙ্গু নদীই ঢালু আকৃতির । সচরাচর এমন নদী আগে কোথাও দেখিনি। নদীটি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে। আর আমরা নদীর বুকে নৌকা দিয়ে যেন সমতল হতে পাহাড়ের চূড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি! নদীতে অনবরত স্রোত বয়ে যাচ্ছে।
প্রায় দেড় ঘন্টা পর আমরা রাজা পাথরের কাছে পৌঁছাই। রাজা পাথর সত্যিই রাজা! তার সাথে আর অন্য কোন পাখরের তুলনাই হয়না! এতোবড় পাথর এই প্রথম দেখলাম। প্রথম দেখাতেই চক্ষু-চড়কগাছ! রাজা পাথরের অবস্থান থানচির তিন্দু ইউনিয়নের সাঙ্গু নদীকে বুকে। রাজা পাথরের দু’পাশে সুউচ্চ ত্যাছ্ড়া ও খাড়া পাথরের পাহাড়। আর সেই পাহাড়ের তলদেশে সগৌরবে অবস্থান করছে রাজা পাথর। আজও স্থানীয় আদিবাসীরা মনে করেন, রাজা পাথর জীবন্ত। তাদের মতে কেউ যদি এই পাথরকে অসম্মান করে তবে রাজা তাতে ক্ষিপ্ত হন এবং তাকে মেরে ফেলেন। এজন্য তারা সেখনে নিয়মিত দুধ ঢেলে, ধূপারতি দিয়ে মোমবাতি জ্বালায়; পূজা করে। রাজা পাথরের সংস্পর্শে এসে আমার নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। বারবার ভাবতে লাগলাম, এ আমি কোথায় এলাম! এ কি সত্যিই আমাদের বাংলাদেশ! গর্ব হচ্ছিল এই ভেবে যে, এই বাংলাদেশের জন্যই আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম! এই বাংলাদেশের জন্যই আমরা এক সাগড় রক্ত দিয়েছিলাম। আমি মনের অজান্তেই আওড়াতে লাগলাম, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি! রাজা পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে আমি রয়েছি স্বপ্নালোকে। রাজা পাথরকে ভুলে থাকা প্রায় অসম্ভব! ঘোর লেগে থাকা সেই দৃশ্য আমার হৃদয় থেকে হয়তো কোনদিনই মুছবে না! রাজা পাথর থেকে ফিরে এসে আমরা গেলাম থানচি শান্তিরাজ ধর্মপল্লীতে। সেখানে দুপুরের আহার শেষে মিশন ক্যাম্পাস ঘুরাঘুরি করলাম বেশ কিছুক্ষণ। থানচি গির্জাটিও একটি টিলার উপর। টিলা মানে ছোটখাট এক ধরণের পাহাড়। দুপুরের পর আমরা থানচি হতে গেলাম বলিপাড়া ধর্মপল্লীতে। তখনো সূর্য ডোবেনি। বলিপাড়া ধর্মপল্লীটি সাঙ্গু নদীর ওপারে। অথচ ওপারে যেতে কোন সেতু নেই। তবে বাঁধাই করা ঘাট আছে। আর নদীর বুক চিরে অল্প পানি বয়ে যাচ্ছে। তাতে একজন আদিবাসী বুড়ি নৌকা দিয়ে খেয়া পাড়াপাড় করছে। আমরাও বুড়ির নৌকাতেই পাড় হলাম। নদীর তীর হতে একটু হেঁটে সামনে গেলেই বলিপাড়া গির্জা। ইতোমধ্যে সূর্যটা ডুবে গেছে। পাহাড়ি প্রকৃতিতে নেমে এসেছে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। বলিপাড়া গির্জার পাশে বৌদ্ধ মন্দিরে সন্ধ্যার মন্দিরা বাজছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ছাত্ররা গেরুয়া কাপড় পড়ে মন্দিরে প্রবেশ করছে। দোতলা বৌদ্ধ মন্দির। মন্দির পেড়িয়ে কয়েক কদম হাঁটলেই বলিপাড়া গির্জা।
গির্জায় গিয়ে দেখলাম হোস্টেলের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার জন্য গির্জা ঘরে যাচ্ছে। বলিপাড়া গির্জাটি বান্দরবান জেলায় হলেও অন্যান্য এলাকা হতে এই এলাকাটি একটু সমতল ধাচের। সহজে বোঝার কোন উপায় নেই যে, এটি পাহাড়ি এলাকার একটি গির্জা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেলে পর আমরা আবার রওনা হলাম বান্দরবান গির্জার উদ্দেশ্যে। পাহাড়ি সন্ধ্যার দৃশ্য বেশ মনোরম ও উপভোগ্য। যাবার সময়ে কিছু কিছু পাড়া ও জন-মানব রাস্তার ধারে চোখে পড়েছিল। ফেরার পথে করোর কোন দেখা নেই। তবে আকাশে ছিল একফালি রুপালি চাঁদ। আমরা চান্দের গাড়িতে ছুটে চলছি। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাঁদও যেন ছুটে চলছে। কোথও থামবার কোন ইয়াত্তা নেই। কেবল দৌঁড় আর দৌঁড়। অবশেষে আমরা বান্দরবান গির্জা ক্যাম্পাসে পৌঁছলাম। রাত তখন বেশ গড়িয়ে গেছে। পরদিন সকালে নাস্তা সেড়ে আমরা বান্দরবান ধর্মপল্লীর উপকেন্দ্র রোয়াংছড়ি বেড়াতে যাই। সেখানে এসএমআরএ সিস্টারগণ হোস্টেলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমাদেরকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আমরা গাড়ি থেকে নামা মাত্রই শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় গান গেয়ে ও ফুল ছিটিয়ে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। এরপর সেখানে শিশুদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হল। আদিবাসী ছোট্ট ছোট্ট ভাই-বোনদের সৃজনশীল ও মৌলিক প্রতিভা এবং পরিবেশনায় আমরা মুগ্ধ-বিষ্মিত না হয়ে পারিনি। দুপুরে আমরা পরিদর্শন করেছি বান্দরবানের বুদ্ধ ধাতু জাদী বা স্বর্ণ মন্দির। স্বর্ণ মন্দিরটি বান্দরবান শহরের বালাঘাটা এলাকার পুরপাড়ায় একটি সুইচ্চ পাহাড়ের চূড়ায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভেন ইউ পান্নইয়া জোতা মাহাথেরো একুশ শতকের প্রারম্ভে এটি নির্মাণ করেন।
স্বর্ণ মন্দিরের পাহাড়ের চূড়ায় একটি গোলাকার পুকুর। পুকুরটির নাম দেবতা পুকুর। দেবতা পুকুরটি সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে সাড়ে তিনশো ফুট উঁচুতে হলেও তাতে সব মৌসুমেই পানি থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভান্তদের মতে, পুকুরটি দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত, তাই এখানে সব সময় পানি থাকে। স্বর্ণ মন্দিরটিতে সব ধরণের মানুষের ভীড় লেগেই আছে। আসলে স্বর্ণ মন্দিরটি একটি বৌদ্ধ মন্দির। মন্দিরের ভেতরে রয়েছে গৌতম বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন সোনালী মূর্তি। বুদ্ধ মূর্তিটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বুদ্ধ মূর্তি। মন্দিরের বাইরের অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে তিব্বত, চীন, নেপাল, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ভূটান, মিয়ানমার ও জাপান দেশের শৈলীতে নির্মিত ১২টি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি এখানে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মন্দিরটিকে স্বর্ণ মন্দির বলা হয় কারণ সম্পূর্ণ মন্দিরই সোনালী প্রলেপ দিয়ে মোড়ানো। মন্দিরের পেছন দিকে ঝুলানো রয়েছে বিশালাকৃতির পিতলের একটি ঐতিহাসিক ঘন্টা। স্বর্ণ মন্দির থেকে নেমে আমরা গেলাম মেঘনা পর্যটন কমপ্লেক্সে। স্বভাবতই বান্দরবানে আগত পর্যটকদের জন্য মেঘনা পর্যটন কেন্দ্র একটি অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন কমপ্লেক্স। বান্দরবান শহর থেকে ৪.৫ কিলোমিটার দূরে এই কমপ্লেক্সে রয়েছে চিত্ত-বিনোদনের নানাবিধ উপকরণ। এখানে রাস্তা হতে পাহাড়ের ঢালুতে নির্মিত সিঁড়ি মাড়িয়ে নিচে নেমে যেতে হয়। নিচে রয়েছে পাহাড়বেষ্টিত স্বচ্ছ জলের একটি মনোরম হ্রদ। হ্রদের উপর ঝুলন্ত সেতু। আর হ্রদের জলে প্যাডেল-বোট।
মেঘনা কমপ্লেক্সের ভেতর উঁচু নিচু পাহাড়ের মাঝে মাঝে রয়েছে শিশু পার্ক, সাফারী পার্ক, চিড়িয়াখানা, পিকনিক স্পট ইত্যাদি। শেষ বিকেলে আমাদেরকে নিয়ে চান্দের গাড়ি ছুটে চললো নীলাচলের দিকে। মেঘনার নিকটবর্তী আরেকটি মনোরম স্থানের নাম নীলাচল। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে দুই হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত নীলাচল বান্দরবান শহর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে টাইগার পাড়ার পাহাড়ের চূড়ায়। বাংলাদেশের মানুষ নীলাচলকে বিভিন্ন নামে ভূষিত করে থাকে। যেমন: বাংলার দার্জিলিং নীলাচল, স্বর্গভূমি নীলাচল, মেঘের রাজ্য নীলাচল ইত্যাদি। নীলাচল থেকে পুরো বান্দরবানকে পাখির চোখে দেখা যায়! বর্ষা, শরৎ কি হেমন্ত, তিন ঋতুতেই এখানে মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটা যায়। হাত বাড়িয়ে মেঘ-মালা স্পর্শ করা যায়। শীতের সকালে পুরো নীলাচল ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে। আমরা গিয়েছি শীতের মেঘমুক্ত শেষ বিকেলে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সূর্যাস্তের দৃশ্য! নীলাচলের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য উপভোগের কথা না হয় অবর্ণনীয়-ই থাক! আমরা অনেকক্ষণ নীলাচলে অবস্থান করেছি। বর্তমানে নীলাচলে অত্যাধুনিক করুকাজমন্ডিত নানান কটেজ ও রেস্টুরেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। খুব ভাল লাগল, যখন দেখলাম সেখানে একটি খ্রিষ্টান পরিবার নিজেদের একটি রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছে। সেখানে স্বামী-স্ত্রী দু’জনে সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকেন। আমরা সেই রেস্টুরেন্টেই ঘন সন্ধ্যায় হালকা নাস্তা করেছি। নীলাচলের বিভিন্ন পাশ থেকে বান্দরবানের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। চিরসবুজ পাহাড়ের সুনির্মল পাহাড়ি বাতাসের সান্নিধ্যে সমগ্র সত্ত্বায় অবগাহিত হওয়া যায়। পাওয়া যায় প্রকৃতির আধ্যাত্মিকতায় যাপিত জীবনে অসীম পুণ্যের অপূর্ব ছোঁয়া…।
লেখক: পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের সেমিনারীয়ান, পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।